✍️ ড. লোকমান খান
বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্ষমতার মেরুকরণ বিষয়টি নিয়ে ভাবতে গেলে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকার বিপরীত চিত্র আমাদের সামনে আসে। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন দেশের সর্বোচ্চ পদাধিকারী, কিন্তু তাঁর ক্ষমতা প্রায় পুরোপুরি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শনির্ভর। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীই কার্যত সকল নির্বাহী ক্ষমতার ধারক-বাহক। চলুন, সংবিধানের বর্তমান কাঠামোর আলোকে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার পার্থক্য ও এর ফলাফল বিশ্লেষণ করি।
প্রধানমন্ত্রী: বাস্তব নির্বাহী ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু
সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীকে বলা যায় রাষ্ট্রপরিচালনার কেন্দ্রীয় চালিকা শক্তি। বাংলাদেশের সংবিধানে পরিষ্কারভাবে বলা আছে, রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁর কর্তৃত্বে প্রয়োগ হবে। ৫৫(২) অনুচ্ছেদ এই মর্মে প্রধানমন্ত্রীর হাতে নির্বাহী ক্ষমতা অর্পণ করে যে তিনি মন্ত্রিসভার প্রধান হিসেবে সকল নীতিনির্ধারণ ও শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। রাষ্ট্রের প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, অর্থনীতি থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র – এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার ওপর ন্যস্ত। রাষ্ট্রপতি নামমাত্র প্রধান হওয়ায়, বাস্তবে দেশের কর্ণধার হলেন প্রধানমন্ত্রীই।
প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবেই রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হন (অনুচ্ছেদ ৫৬(৩) অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সেই সংসদ সদস্যকেই প্রধানমন্ত্রী করবেন যিনি সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন অর্জন করেন)। এতে রাষ্ট্রপতির নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের অবকাশ থাকেনা – জনগণের ভোটে যে দল ক্ষমতায় এসেছে তার নেতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রধানমন্ত্রী হন। ফলে গণমানুষের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত না হয়েও রাষ্ট্রপতির চেয়ে প্রধানমন্ত্রী অনেক বেশি গণতান্ত্রিক স্বীকৃতি ভোগ করেন, কারণ তিনি জনপ্রতিনিধিদের নেতা। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের পর মন্ত্রিসভা গঠন, দপ্তর বণ্টনসহ সার্বিক সরকার পরিচালনায়ও রাষ্ট্রপতির ভূমিকা ন্যূনতম; সংবিধান অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদেরও রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেন বটে, তবে তা প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তালিকা অনুসারেই ঘটে ।
প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ শুধু রাষ্ট্রপতির কর্মকাণ্ডে নয়, প্রশাসনের সর্বত্র বাধ্যতামূলক। গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদগুলোর নিয়োগপ্রক্রিয়া এর বড় উদাহরণ। প্রধান বিচারপতি নিয়োগ (একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে রাষ্ট্রপতি সামান্য নিজ বিবেচনা প্রয়োগ করতে পারেন) ছাড়া প্রায় সব উচ্চপদে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী নিয়োগ দিয়ে থাকেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সংবিধানে রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতা দেওয়া থাকলেও বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শই চূড়ান্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিচারপতি, অ্যাটর্নি জেনারেল, মহাহিসাবনিরীক্ষক (CAG), পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান – এমন বহু পদের নামমাত্র নিয়োগকারী রাষ্ট্রপতি, কিন্তু নির্ধারক ভূমিকায় থাকেন প্রধানমন্ত্রী। দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজেও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিসভাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, রাষ্ট্রপতির সচিবালয় তা অনুমোদনের জন্য পাঠালে রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিক সিলমোহর দেন।
এছাড়াও, সংসদে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াতেও প্রধানমন্ত্রীর সুবিধাজনক অবস্থান থাকে। কারণ সংসদে তাঁর দল সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকলে আইন পাস করাতে তেমন সমস্যা হয় না। রাষ্ট্রপতির বিল অনুমোদনের ক্ষমতা সীমিত – তিনি বিল ফেরত দিলেও সংসদ পুনরায় পাস করলে সেটি আইনে পরিণত হয়। সংবিধানের বিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি পাঁচ বছরের মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হলেও (সরাসরি জনগণ নয়, সংসদ সদস্যদের ভোটে), প্রধানমন্ত্রী যে কোনো সময় সংসদ ভেঙে দেওয়ার পরামর্শ দিলে রাষ্ট্রপতির তা মানতে হয়। অর্থাৎ, সরকারের আয়ুষ্কাল প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাধীন, রাষ্ট্রপতির নয়। সামগ্রিক চিত্রে দেখা যায়, রাষ্ট্রক্ষমতার প্রায় সব কটি রাশ প্রধানমন্ত্রীর হাতে কেন্দ্রীভূত, যেখানে রাষ্ট্রপতি আছেন একটি সংবিধান-প্রদত্ত সম্মানসূচক অবস্থানে।
অনুচ্ছেদ ৭০: প্রধানমন্ত্রীর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের বয়ান
আমাদের সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টের কাছে দায়বদ্ধ বলে তত্ত্বে বলা হলেও, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ এই দায়বদ্ধতাকে অনেকাংশে নিস্ক্রিয় করে দিয়েছে। অনুচ্ছেদ ৭০ অনুযায়ী, কোনো সাংসদ নিজ দলের বিরুদ্ধে ভোট দিলেই অথবা দল থেকে ইস্তফা দিলেই তাঁর সংসদ সদস্য পদ খারিজ হবে। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কোনো সাংসদ চাইলেও প্রধানমন্ত্রীর (দলনেতার) বিরুদ্ধে আস্থা ভোট আনতে বা তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারবেন না, করলে নিজের আসনটাই হারাবেন। ফলস্বরূপ, সংসদে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের ওপর একটি দলগত নিঃশর্ত আনুগত্য নিশ্চিত হয় – সরকারপ্রধানের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে যাওয়া আইনপ্রণেতাদের পক্ষে অসম্ভব। এটি সরকারকে স্থিতিশীলতা দিলেও একই সাথে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে প্রায় নিঃসন্দেহে স্বৈরাচারী রূপ দিয়েছে বলে সমালোচকরা মনে করেন। অনুচ্ছেদ ৭০ সংসদীয় ব্যবস্থাকে পঙ্গু করেছে এবং সংসদে একধরনের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে কারণ এমপিরা দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে কিছু বলতে বা করতে পারেন না। আসলে দলের প্রধানই যখন সরকার প্রধান, তখন এই ধারা তাঁকে সংসদ থেকে কার্যত অপসারণ-অধ্যাদেশ (impeachment) বা অনাস্থা ভোটের বিরুদ্ধে পূর্ণ সুরক্ষা দেয়। বলা যায়, সংসদও প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায় অনুচ্ছেদ ৭০-এর কারণে, যেহেতু তাঁর দলের বাহিরে গিয়ে কেউ মত দিতে পারে না।
অনুচ্ছেদ ৭০-এর ফলে রাষ্ট্রপতির ভূমিকাও আরো গৌণ হয়ে পড়ে। কেননা, তত্ত্বগতভাবে যদি কোনো প্রধানমন্ত্রী সংসদের আস্থা হারান, রাষ্ট্রপতি তখন বিকল্প সরকার প্রধান খুঁজতে উদ্যোগ নিতে পারতেন। কিন্তু বাস্তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে ভাঙন বা ভিন্নমত প্রকাশ অসম্ভব হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী সংসদে তাঁর অবস্থান মোটামুটি অটুট থাকে পুরো মেয়াদ জুড়ে। রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সংসদে অনাস্থা পরীক্ষার কথা চিন্তা করাও অবাস্তব – কারণ তাঁর কাছে যাওয়ার আগেই সাংসদরা দলীয় হুইপ মেনে চলতে আইনগতভাবে বাধ্য। তাই সংবিধানের এই ধারা প্রধানমন্ত্রীকে আরও শক্তিশালী এবং রাষ্ট্রপতিকে আরও নিস্প্রভ করে রেখেছে। সংসদ নেতা ও প্রধান নির্বাহী – দু’ভূমিকাতেই প্রধানমন্ত্রী একক কর্তৃত্ব বিস্তার করেন এবং সাংবিধানিক কাঠামো তাকে সে সুযোগ নিশ্চিত করেছে।
রাষ্ট্রপতি: প্রতীকী রাষ্ট্রপ্রধানের সীমিত অধিকার
বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষায় রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান এবং “সংবিধান ও আইনে নিহিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব” পালন করবেন। কিন্তু এই কথাটির আড়ালে একটি বড় শর্ত লুকিয়ে আছে: রাষ্ট্রপতিকে তার প্রায় সকল সাংবিধানিক কর্মকাণ্ড প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী করতে হবে। সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, “রাষ্ট্রপতি তাঁর সকল কার্যাবলী প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী পালন করবেন,” দুটি মাত্র ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম – প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ। অর্থাৎ, এসব ছাড়া বাকি প্রতিটি কাজে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর কথামতো চলতে বাধ্য থাকতে হয়।
এমনকি রাষ্ট্রপতির যেসব সাংবিধানিক দায়িত্ব বাইরের চোখে ক্ষমতাধর বলে মনে হয়, সেগুলোও আসলে আনুষ্ঠানিক বা প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাধীন। উদাহরণস্বরূপ, সংসদ অধিবেশন আহ্বান বা ভঙ্গ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে ঠিকই, কিন্তু তা প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শ সাপেক্ষে প্রয়োগ করতে হয়। সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে জাতীয় সংসদে পাস হওয়া বিলসমূহে স্বাক্ষরদানের দায়িত্ব দিয়েছে, তবে সেখানে স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধান্তের সুযোগ নেই – সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিল অনুমোদন করা রাষ্ট্রপতির ঐতিহাসিক রুটিন দায়িত্ব মাত্র। রাষ্ট্রপতি চাইলে কোনো বিল আটকে রাখতে পারেন না, কারণ সংসদ পুনরায় বিল পাস করলে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর দেওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায় (এখানে তাঁর ভেটো ক্ষমতা নেই)। একইভাবে, রাষ্ট্রপতির জরুরি অবস্থা জারির ক্ষমতাও প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি ছাড়া সক্রিয় হয় না; সংবিধানের ১৪১(ক) অনুচ্ছেদে জরুরি অবস্থা ঘোষণার আদেশে প্রধানমন্ত্রীর পূর্বস্বাক্ষর (counter-signature) আবশ্যিক বলে উল্লেখ আছে। অর্থাৎ জাতীয় সংকটকালীন সময়েও রাষ্ট্রপতি স্বতন্ত্রভাবে পদক্ষেপ নিতে পারেন না।
রাষ্ট্রপতির কয়েকটি সাংবিধানিক আবশ্যিক ক্ষমতা রয়েছে বটে: যেমন আদালতে দণ্ডিত ব্যক্তিদের ক্ষমা বা দণ্ড মওকুফ করার ক্ষমতা (প্রেসিডেনশিয়াল প্ররোগেটিভ অফ মারসি) সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদে প্রদান করা হয়েছে, এবং সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদটি নামমাত্রভাবে রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত (অনুচ্ছেদ ৬১)। কিন্তু এখানেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন। উপরের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে ক্ষমা প্রদান করাও রাষ্ট্রপতির “স্বতন্ত্র” ক্ষমতা নয় – তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ীই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হলেও “আইনের দ্বারা সেই ক্ষমতার প্রয়োগ বিধিবদ্ধ” বলে উল্লেখ আছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত বাস্তব সিদ্ধান্ত সরকারই নেয়, রাষ্ট্রপতি নন। রাষ্ট্রপতির ভূমিকা আসলে প্রতীকী প্রধানের, যাঁর নামে সকল সরকারি আদেশ জারি হয় কিন্তু সিদ্ধান্ত আসে অন্য জায়গা থেকে। সংবিধানের ৫৫(৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারী সকল নির্বাহী কার্যক্রম রাষ্ট্রপতির নামে প্রকাশিত ও সম্পাদিত হবে বলে লেখা আছে, যা বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে: রাষ্ট্রপতির নাম ব্যবহার করা হয় মাত্র, কিন্তু কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর। সংসদে দেওয়া রাষ্ট্রপতির বার্ষিক ভাষণ থেকে শুরু করে বিদেশি রাষ্ট্রদূত গ্রহণ, মন্ত্রীদের শপথবাক্য পাঠ করানো – এসব আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব রাষ্ট্রপতি পালন করেন বৈকি, তবে কোনোটিই বাস্তব নীতিনির্ধারণী ক্ষমতার পরিচায়ক নয়।
প্রশ্ন আসে, রাষ্ট্রপতি কি তাহলে সম্পূর্ণই নির্বাক ও নিস্ক্রিয় একজন ক্ষমতাহীন পদ? সাধারণ পরিস্থিতিতে হ্যাঁ – বাংলাদেশের সাংবিধানিক কাঠামো তাকে এক প্রকার “অনুগৃহীত সাংবিধানিক অভিভাবক” হিসেবে দাঁড় করিয়েছে, যার প্রধান কাজ হচ্ছে সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী অনুষ্ঠানিকতা পালন করা। সংবিধানের ৪৮(৫) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতিকে দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে অবহিত থাকার অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং রাষ্ট্রপতি চাইলে কোনো বিষয় মন্ত্রিসভায় আলোচনার জন্য প্রস্তাব করতে পারেন। কিন্তু এই অধিকার কাগজে-কলমে সীমিত – ব্যতিক্রমী সংকটের সময় হয়তো রাষ্ট্রপতির অভিজ্ঞতা বা “মোরাল অথরিটি” দিয়ে সরকারকে পরামর্শ দিতে পারেন, কিন্তু সেটা বাধ্যতামূলক নয়। সংবিধান বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে সামান্য বিচার-বিবেচনার সুযোগ দিয়েছে, যেমন প্রধানমন্ত্রী পদ শূন্য হলে নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের সময় যদি সংসদে কোনো দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্পষ্ট না থাকে তখন রাষ্ট্রপতিকে নিজের বিচারশক্তি দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আবার, প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সংসদের আস্থা না থাকলে তিনি সংসদ ভেঙে দিতে পরামর্শ দিলে রাষ্ট্রপতি বিকল্প কোনো নেতা দিয়ে সরকার গঠন সম্ভব কি না ভেবেই পদক্ষেপ নেবেন (অনুচ্ছেদ ৫৭(২) অনুযায়ী)। তবে এসব ক্ষেত্র খুবই বিরল এবং সীমিত। বাস্তবে রাষ্ট্রপতির অধিকাংশ পদক্ষেপই প্রধানমন্ত্রীর “ইচ্ছায়” নির্ধারিত হয়। এক কথায়, বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট পদটি “সার্বভৌম সম্মানের” হলেও কার্যক্ষমতায় অনেকটা শূন্যপদতুল্য।
উপসংহার: ভারসাম্যহীন ক্ষমতার প্রতিচ্ছবি
বাংলাদেশের সংবিধান প্রবর্তনকালে সংসদীয় গণতন্ত্রকে অগ্রাধিকার দিয়ে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার এই বিভাজনটি নির্ধারিত হয়েছিল। বাস্তবে সেটি আজ এমন এক কাঠামো তৈরি করেছে যেখানে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন সকল ক্ষমতার কেন্দ্র, আর রাষ্ট্রপতি রয়েছেন অলংকারমাত্র। বর্তমান সাংবিধানিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি প্রায় “বাধ্য কিং-এর মতো” – সিংহাসনে বসে আছেন, কিন্তু হাত-পা বাঁধা অবস্থায়; আর প্রধানমন্ত্রী কার্যত “নির্বাহী রাজা বা রাণী” – যাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়। সংবিধানের ভাষায় ও চেতনায় রাষ্ট্রপতির গৌরবময় ভূমিকা থাকলেও বাস্তব ক্ষমতায়নের অভাব আমাদের গণতন্ত্রের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এই ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার পক্ষ-বিপক্ষ দুইদিকেই যুক্তি আছে। একদিকে, এমন কাঠামো সরকারকে স্থিতিশীলতা দেয় – নির্বাচিত সরকারের প্রধান নির্বাহী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এককেন্দ্রিকভাবে কাজ করতে পারেন, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দ্বৈত ক্ষমতার দ্বন্দ্ব হয় না। অন্যদিকে, প্রায় অপরীক্ষিত ও অবারিত ক্ষমতা দীর্ঘমেয়াদে স্বেচ্ছাচারের ঝুঁকি বাড়ায়, গণতন্ত্রের স্বাভাবিক জবাবদিহিতা কমিয়ে দেয়। বিশেষ করে অনুচ্ছেদ ৭০-এর কড়াকড়িতে প্রধানমন্ত্রীকে কার্যত পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ থেকেও মুক্ত মনে হতে পারে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন তুলতেই পারে।
শেষ পর্যন্ত, আমাদের সংবিধানই আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চরিত্র নির্ধারণ করেছে। এটি এমন এক ছবি এঁকেছে যেখানে রাষ্ট্রপতির মর্যাদা আছে কিন্তু ক্ষমতা নেই, আর প্রধানমন্ত্রীর বিপুল ক্ষমতা আছে কিন্তু তার জবাবদিহি খুবই সীমিত পরিসরে, নাই বললেই চলে। এই কাঠামো আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিশেষ বাস্তবতা তুলে ধরে। বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির ভূমিকাকে প্রায় রাজসিক আলংকারিক স্তরে নামিয়ে এনে এবং প্রধানমন্ত্রীর হাতে ভারসাম্যহীন ক্ষমতা দিয়ে রাখার সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে চিন্তা করা জরুরি। সংবিধানের বর্তমান ধারাগুলো স্পষ্টতই জানাচ্ছে – প্রধানমন্ত্রীই সকল ক্ষমতার অধিপতি, আর রাষ্ট্রপতি তাঁর ছায়াসঙ্গী মাত্র। ভবিষ্যতে যদি ক্ষমতার ভারসাম্যে কোনো পরিবর্তন আনা হয়, তাহলে সংবিধান সংশোধন ছাড়া উপায় নেই। তবে আপাতত, আমাদের সংবিধান যে ক্ষমতার চিত্রকল্প এঁকেছে, সেখানে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা ভারসাম্য রক্ষাকারী নয় বরং রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতার অভিভাবক, আর প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা কার্যকর শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত – এটাই বাংলাদেশের সংবিধান-স্বীকৃত বাস্তবতা।
শেষ কথা
বর্তমান সংবিধানের কাঠামো তাই কেবল ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা নয়, বরং স্বৈরতন্ত্রের বীজ বপন করে রেখেছে। যেখানে রাষ্ট্রপতির হাতে নেই কোনো কার্যকর নিয়ন্ত্রণ, সংসদীয় সদস্যরা অনুচ্ছেদ ৭০-এর কারণে বন্দি, আর প্রধানমন্ত্রী কার্যত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী – সেখানে গণতন্ত্র কাগজে-কলমে টিকে থাকলেও বাস্তবে এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসন গড়ে ওঠে। ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে, এককেন্দ্রিক ক্ষমতা অবশেষে একনায়কতন্ত্রে রূপ নেয়। তাই সংবিধান অপরিবর্তিত রাখলে ভবিষ্যতেও আবার স্বৈরশাসনের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। বাংলাদেশকে সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে বড় ধরনের সংশোধন, বা তার চেয়েও ভালো সমাধান হবে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন, যেখানে ক্ষমতার ভারসাম্য, জবাবদিহি ও জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।



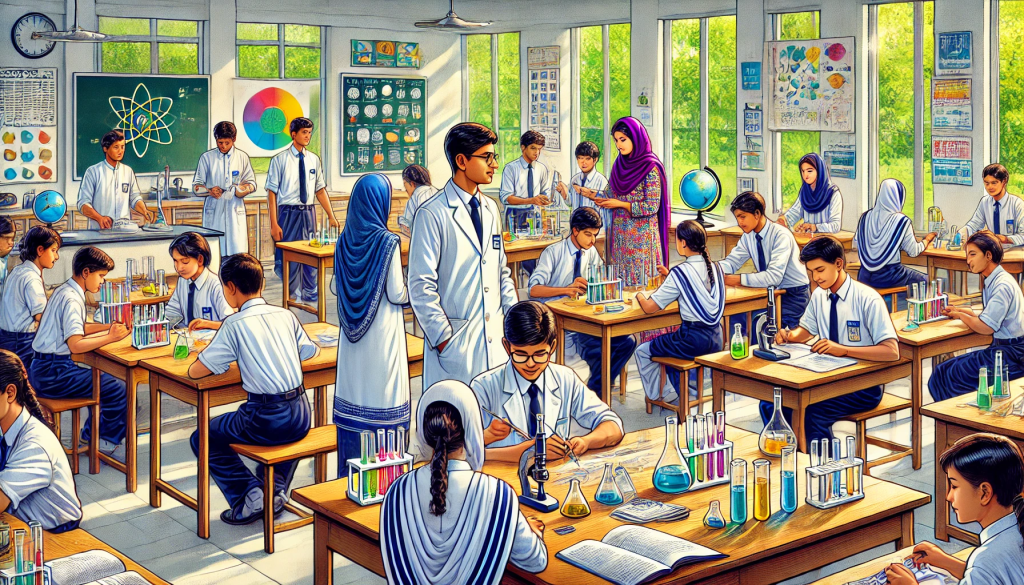


Leave a comment